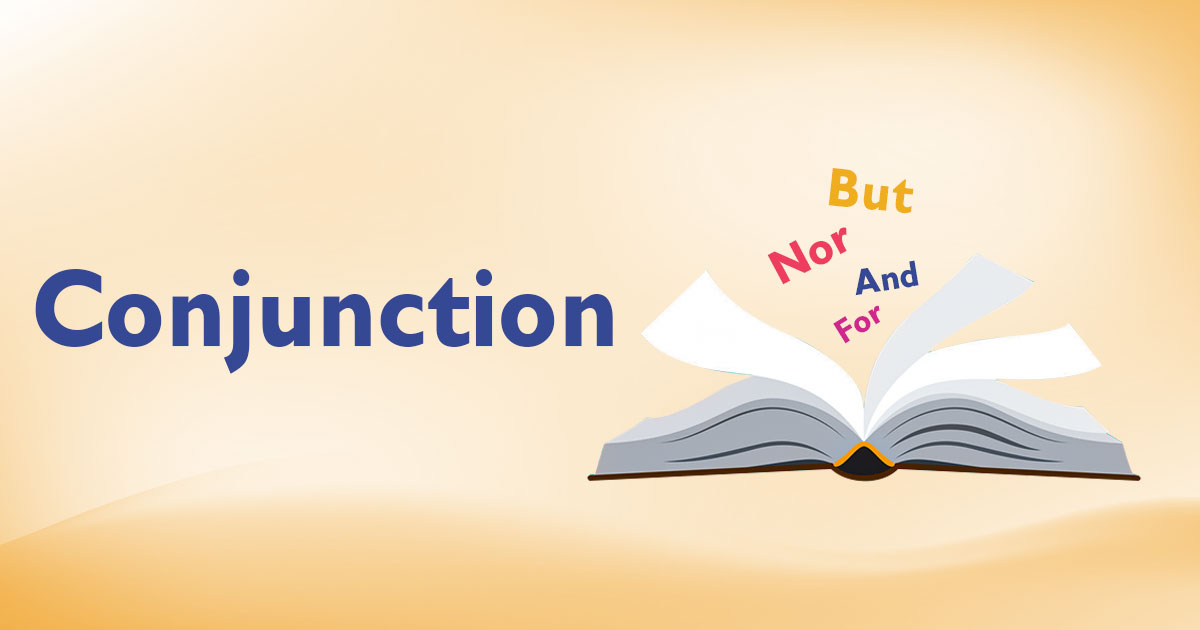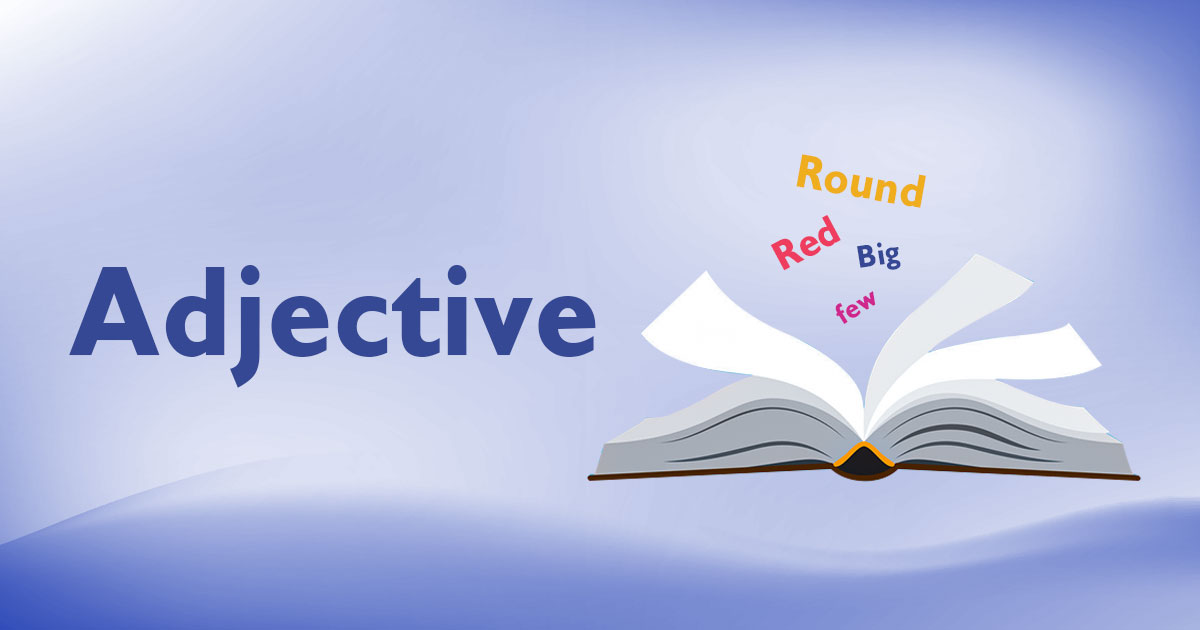হাইড্রা (Hydra)
Hydra হচ্ছে Cnidaria (নিডারিয়া) পর্বের একটি জলজ প্রানী। এর দেহ সরল, অর্থাৎ অল্প কয়েকটি অঙ্গ দিয়েই হাইড্রা তার দেহের সব কাজ করে থাকে। এটি দ্বিস্তরী প্রাণীর এক আদর্শ উদাহরণ।
হাইড্রার শ্রেণিবিন্যাস:
Kingdom: Animalia
Phylum: Cnidaria
Class: Hydrozoa
Order: Hydroida
Family: Hydridae
Genus: Hydra
Species: Hydra vulgaris
বর্তমানে পৃথিবীতে চল্লিশ প্রজাতির হাইড্রা আছে। তবে বাংলাদেশে কেবল তিনটি প্রজাতি পাওয়া গেছে। প্রথম যে প্রজাতিটির নাম Pelmatohydra oligactis, এটি বাদামী বর্নের হয়ে থাকে। অপর প্রজাতিটির নাম Hydra Vulgaris, যা বর্ণহীন বা হলুদ বর্ণের হয়ে থাকে। এবং তৃতীয় যে প্রজাতিটি আমাদের দেশে দেখতে পাওয়া যায় তা হলো Chlorohydra viridissima এরা সাধারণত সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে।
হাইড্রার বাসস্থান
হাইড্রা মুক্তজীবী প্রাণী, অর্থাৎ এরা স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় । স্থির, শীতল ও পরিষ্কার পানিতে এদের বেশি দেখা যায়। ঘোলা, উষ্ণ ও চলমান পানিতে এদের কম দেখা যায়।
হাইড্রার স্বভাব
হাইড্রার একটি প্রধান স্বভাব হলো, ক্ষুধার্ত অবস্থায় এর দেহ ও কর্শিকা, সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয়ে পানিতে দুলতে থাকে। হাইড্রা অন্য কোনো প্রানী খেয়ে জীবন ধারণ করে, তাই একে মাংসাশী প্রানী বলা হয়। হাইড্রা তার দেহে থাকা কর্ষিকার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে।
খাদ্য গ্রহণের মতো করে চলফেরার জন্যও হাইড্রা কর্ষিকার সাহায্য নেয়। তবে কতদূর যাবে তার উপর depend করে, এর চলন পদ্ধতি আলাদা আলাদা হয়। মুকুলোদগম ও দ্বিবিভাজনের মাধ্যমে অযৌন জনন. রূপকথার দানবের যেমন মাথা কেটে দিলে, সেখান থেকে আবার নতুন করে মাথা জন্মায়। হাইড্রার ক্ষেত্রে তা দেখা যায়, সে তার হারানো বা ক্ষতিগ্রস্থ অংশ পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে।
হাইড্রার আকার-আকৃতি
হাইড্রার দেহ নরম ও নলাকার। মুখের এক প্রান্ত খোলা ও অপর প্রান্ত বন্ধ। খোলা প্রান্তে মুখছিদ্র ও বন্ধ প্রান্তটি কোনো বস্তুর সাথে যুক্ত থাকে। দেহ অরীয় প্রতিসম অর্থাৎ এর দেহকে মাঝ বরাবর কেটে সমান দুইের বেশি সংখ্যক ভাগে ভাগ করা যাবে । এটি ১০ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত লম্বা ও প্রায় ১ মিলিমিটার পর্যন্ত চওড়া হয়ে থাকে। একটি পরিণত হাইড্রার দেহকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়ঃ
১. হাইপোস্টোম
দেহের যে মুক্ত প্রান্ত মোচাকৃতির, ছোট ও সংকোচন-প্রসারনশীল, এবং চূড়ায় বৃত্তাকার মুখছিদ্র বিদ্যমান এই ছিদ্র পথে খাদ্য গৃহীত হয় ও অপাচ্য অংশ বহিষ্কৃত হয় তাকে হাইপোস্টোম বলে।
২. দেহকান্ড
হাইপোস্টোমের নিচ থেকে পাদ-চাকতির উপর পর্যন্ত সংকোচন-প্রসারণশীল অংশটি হচ্ছে দেহকান্ড বা Trunk। দেহকান্ড তিন প্রকার:
ক) কর্ষিকা
হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিক ঘিরে ছয় থেকে দশটি সরু, সংকোচনশীল, দেহ থেকে লম্বা ও ফাঁপা সুতার মতো কর্ষিকা থাকে। কর্ষিকার বাহিরের প্রাচীরে ছোট টিউমারের মতো অসংখ্য Nematocyst battery থাকে। প্রত্যেক ব্যাটারীতে থাকে বিভিন্ন ধরণের নেমাটোসিস্ট। এই কর্ষিকা ও নেমাটোসিস্ট সবসময় একসাথে কাজ করে।
কর্ষিকার কাজঃ
- খাবার সংগ্রহ
- চলন
- আত্মরক্ষায় অংশগ্রহণ করা।
খ) মুকুল
গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত খাবার পেলে মুকুল সৃষ্টির অনুকূল সময় তৈরি হয়। এই পরিবেশে দেহের প্রায় মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে এক বা একের বেশি মুকুল বের হয়।
মুকুলের কাজ
মুকুলের প্রধান কাজ নতুন নতুন হাইড্রা সৃষ্টি। এই পদ্ধতিটি হাইড্রার অন্যতম অযৌন জনন পদ্ধতি।
গ) জননাঙ্গ
হেমন্ত ও শীতকালে দেহকান্ডের উপরের অংশে এক বা একাধিক কোণাকার শুক্রাশয় দেখা যায়। এছাড়া নিচের অংশে এক বা একাধিক গোলাকার ডিম্বাশয় নামক অস্থায়ী জননাঙ্গ দেখা যায়।
জননাঙ্গের কাজ
জননাঙ্গের প্রধান কাজ হল যৌন জননে অংশগ্রহন করা।
৩. পদতল বা পাদ-চাকতি
দেহকান্ডের নিচের প্রান্তে অবস্থিত, গোল ও চাপা অংশটিকে পাদ-চাকতি বা pedal disc বলে।
পাদ-চাকতির কাজ:
- এক ধরনের আঠালো রস ক্ষরণ করে যার সাহায্য প্রানি যে কোনো তলের সাথে আটকে থাকে।
- এক ধরনের বুদবুদ বা bubble সৃষ্টি করে যা প্রাণীকে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করে।
- চাকতির ক্ষনপদ সৃষ্টিকারী কোষের সাহায্যে গ্লাইডিং চলন সম্পন্ন হয়।
Hydra দ্বিভ্রূণস্তরী (diploblastic) প্রাণী অর্থাৎ ভ্রুণ অবস্থায় এদের দেহ প্রাচীরের কোষগুলো কেবল এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে সাজানো থাকে।
পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে এক্টোডার্ম এপিডার্মিসে এবং এন্ডোডার্ম গ্যাস্ট্রোডার্মিস-এ পরিণত হয়। অর্থাৎ এক্টোডার্ম পরিণত হবে এপিডার্মিসে, আর এন্ডোডার্ম পরিণত হবে গ্যাস্ট্রোডার্মিসে।
এই দুই স্তরের মাঝখানে জেলির মতো একটি স্তর থাকে। যাকে মেসোগ্লিয়া বলে। এটি কোষস্তরের ভিত্তিরূপে কাজ করে।
হাইড্রার অন্তর্গঠন
হাইড্রার দেহ মূলত দেহপ্রাচীর ও কেন্দ্রীয় পরিপাকসংবহন গহ্বর (Gastro vascular cavity) বা সিলেন্টেরন (Coelenteron) নিয়ে গঠিত। আবার কাজের ভিন্নতা অনুযায়ী হাইড্রার এপিডার্মিসের কোষের গঠনে বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। এটি একটি পাতলা কিউটিকলে আবৃত। এপিডার্মিস কোষ হাইড্রার বাইরের দিকের আবরণ গঠন করে।
Hydra-এর দেহপ্রাচীরের কোষসমূহ
এপিডার্মিস
১. পেশি-আবরণী কোষ
২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
৩. সংবেদী কোষ
৪. স্নায়ু কোষ
৫. গ্রন্থি কোষ
৬. জনন কোষ এবং
৭. নিডোসাইট
মেসোগ্লিয়া- কোন কোষস্তর নয়, একে সংযোগকারী স্তর বলা হয়।
গ্যাস্ট্রোডার্মিস
১. পুষ্টি কোষ
২. গ্রন্থি কোষ
৩. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ,
৪. সংবেদী কোষ এবং
৫. স্নায়ু কোষ
হাইড্রার এপিডার্মিস সাত ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত
১. পেশী আবরণী কোষ
পেশী আবরণী কোষ এপিডার্মিসের সম্পুর্ণ অংশ জুড়ে পেশী আবরণী কোষের অবস্থান। বাহিরের দিকে চওড়া ও ভেতরের দিকে সরু প্রান্তবিশিষ্ট এ কোষগুলো দেখতে কোণাকার। কর্ষিকায় কোষগুলো বেশ বড় ও চাপা এবং কয়েকটি করে নিডোব্লাস্ট (পরিস্ফুটনরত নিডোসাইট) ধারণ করে।
কাজ:
- দেহাবরণ সৃষ্টি করে দেহকে রক্ষা করে।
- সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে পেশির মতো কাজ করে।
২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
পেশি-আবরণি কোষের ভেতরের দিকে সরু প্রান্তের ফাঁকে ফাঁকে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ গুচ্ছ আকারে থাকে। মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে এসব কোষ অবস্থান করে। এগুলো গোল বা তিনকোণা হতে পারে। এদের সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস দেখা যায়, এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা মসৃ্ণ। আবার রাইবোজম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়াও থাকে।
কাজ:
- এসব কোষ প্রয়োজনে অন্য যে কোনো ধরনের বহিঃত্বকীয় কোষে পরিণত হয়।
- পুনরুৎপত্তি ও মুকুল সৃষ্টিতে অংশ নেয় এবং
- কিছুদিন পরপর অন্যান্য কোষে পরিণত হয়ে দেহের পুরনো কোষের স্থান পূরণ করে।
৩. সংবেদী কোষ
সংবেদী কোষগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে সমকোণে, অর্থাৎ নব্বই ডিগ্রী কোণে এলোমেলোভাবে ছড়ানো থাকে। তবে এদেরকে কর্ষিকা, হাইপোস্টম ও পদতলের চারদিকে বেশি দেখা যায়।
কাজ:
- পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা (যেমন আলো, তাপ প্রভৃতি) গ্রহণ করে স্নায়ুকোষে সরবরাহ করে।
৪. স্নায়ু কোষ
স্নায়ু কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, সঠিক আকার নেই এবং একে অপরের সাথে মিলে স্নায়ু জালিকা গঠন করে।
কাজ:
- সংবেদী কোষ, সংগৃহীত উদ্দীপনা দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করা।
৫. গ্রন্থি কোষ
গ্রন্থি কোষ ক্ষরণকারী দানাবিষিষ্ট এক ধরনের পরিবর্তিত লম্বাকার এপিডার্মাল কোষ। মুখছিদ্রের চারদিকে ও পাদ-চাকতিতে প্রচুর গ্রন্থি কোষ দেখা যায়।
কাজ:
- মিউকাস ক্ষরণ করে দেহকে কোনো বস্তুর সঙে লেগে থাকতে সাহায্য করে।
- বুদবুদ সৃষ্টি করে ভাসতে সাহায্য করে।
- ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে চলনে অংশগ্রহণ করে
- মুখছিদ্রের গ্রন্থিকো্ষ ক্ষরণ এবং খাদ্য গলাধঃকরণে সাহায্য করে।
৬. জনন কোষ
হাইড্রার দেহে জননকোষ দু’ধরনের যেমন শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। পরিণত শুক্রাণু অতি ক্ষুদ্র এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত। পরিণত ডিম্বাণুটি বড় ও গোল।
কাজঃ
- যৌন জননে অংশগ্রহণ করে।
৭. নিডোসাইট কোষ
হাইড্রার পদতল ছাড়া বহিঃত্বকের সব জায়গায় বিশেষ করে কর্ষিকার পেশি-আবরণি কোষের ফাঁকে ফাঁকে নিডোসাইট থাকে। এটি কোষের মুক্তপ্রান্ত্রে সংবেদী নিডোসিল (Cnidocil) এবং ভিতরের দিকে প্যাঁচানো সুতাযুক্ত নেমাটোসিস্ট বহন করে।
আদর্শ নেমাটোসিস্টের সুতার গোড়ায় ৩টি বড় কাঁটার মতো বার্ব (Barb) থাকে এবং গহ্বরটি হিপ্নোটক্সিন (Hypnotoxin) নামক বিষাক্ত রসে পূর্ণ। পরিস্ফুটনরত নিডোসাইটকে নিডোব্লাস্ট (Cnidoblast) বলে।
কাজ:
- নিডোসাইটের নেমাটোসিস্ট অঙ্গানু প্রাণীর খাদ্য গ্রহণে ব্যবহৃত হয়।
- নেমাটোসিস্ট প্রাণীর চলন ও আত্ত্বরক্ষায় সাহায্য করে।
আদর্শ নিডোসাইটের বিভিন্ন অংশ
হাইড্রার সবচেয়ে গুরুত্ত্বপূর্ণ ও বহুল ব্যবহৃত কোষ নিডোসাইট। একটি আদর্শ নিডোসাইট পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত।
- আবরণ- নিডোসাইট এর প্রতিটি কোষ দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত অর্থাৎ কোষে দুটি স্তর থাকে।
- নেমাটোসিস্ট- নিডোসাইটের অভ্যন্তরে অবস্থিত সূত্রকযুক্ত একটি ক্যাপসুলের নাম নেমাটোসিস্ট। আদর্শ নিডোসাইটে ক্যাপসুলটি বিষাক্ত তরল হিপনোটক্সিন (Hypnotoxin)-এ পূর্ণ থাকে।
- অপারকুলাম- স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও ক্যাপসুল যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে তার নাম অপারকুলাম।। উন্মুক্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়।
- নিডোসিল- নিডোসিল ট্রিগারের মতো কাজ করে, ফলে অপারকুলাম সরে যায়, এবং প্যাঁচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে।
- পেশিতন্তু ও ল্যাসো- নিডোসিল ট্রিগারের মতো কাজ করে, ফলে অপারকুলাম সরে যায়, এবং প্যাঁচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে।
নেমাটোসিস্টের প্রকারভেদ
নিক্ষিপ্ত সূত্রকের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী ভার্নার ১৯৬৫ সালে, নিডারিয়া জাতীয় প্রাণিদের দেহ থেকে, ২৩ ধরনের নেমাটোসিস্ট শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে চার ধরনের নেমাটসিস্ট হাইড্রায় পাওয়া যায়।
- স্টিনোটিল বা পেনিট্র্যান্ট- হাইড্রার চার ধরনের নামাটোসিস্টের মধ্যে এই ধরনের নেমাটোসিস্টই সবচেয়ে বড়। পেনিট্যান্ট নিমাটোসিস্টের বাল্ব সর্বাপেক্ষা বড় ও ফেনোল এবং আমিষের সমন্বয়ে গঠিত হিপ্নোটক্সিন রস দ্বারা পূর্ণ থাকে। সূত্রকটি লম্বা ও নলাকার। সূত্রকের স্ফীত গোড়াকে বাট বা শ্যাফট (Butt বা Shaft) বলে। এদের সূত্রকের গোড়াটা স্ফীত এবং গোড়ায় ৩টি বড় কাঁটা বা বার্ব (Barb) এবং ৩ সারি ছোট কাটা বা বার্বিউল (Barbule) থাকে। সূত্রকের অগ্রপ্রান্ত খোলা এবং দেহ কন্টকবিহীন।
কাজঃ এই নিমাটোসিস্টের বার্বগুলি শিকারের গায়ে বিদ্ধ হয়। এদের বার্বিউল ও সূত্রক শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে এবং হিপ্নোটক্সিন প্রয়োগ করে শিকারকে অবশ করে ফেলে বা মেরে ফেলে।
- ভলভেন্ট- এসব নিমাটোসিস্টের থলিটা ক্ষুদ্র, গোলাকার এবং সুত্রকের গোড়ায় স্ফীতি নাই এবং দেহে কোন কন্টক থাকে না। ব্যবহারের পূর্বে বা বিশ্রামরত অবস্থায় সূত্ৰকটা কর্কের স্ক্রুর মতো প্যাচান অবস্থায় থলির ভিতর অবস্থান করে। সূত্রকের অগ্রভাগ বন্ধ।
কাজঃ শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে এবং চলনে সহায়তা করে।
- স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট- এসব নিমাটোসিস্টের থলি ছোট, এবং সূত্রকের গায়ে ছোট কাটা বা বার্বিউল থাকে। সূত্রকের মুক্ত প্রান্ত খোলা।সূত্রকের গোড়ায় বাট বা স্ফীতি এবং বার্ব নাই।
কাজ : স্ট্রেপটোলিন গুটিন্যান্ট সূত্রকের সাহায্যে শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে। এরা চলনে সহায়তা করে।
- স্ট্রেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট- এসব নিমাটোসিস্টের বাল্ব ছোট, সূত্রকের দেহ কন্টকবিহীন। সূত্রকের গোড়ায় স্ফীতি বা বাট (Butt) নাই, সূত্রকের গায়ে বার্ব ও বার্বিউল নাই।
কাজ: উভয় ধরনের গুটিন্যান্ট প্রধানতঃ শিকার ধরায় ও চলনে অংশ নেয়।
নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষপণ কৌশল
নেমাটোসিস্টের সূতা নিক্ষেপের কৌশল অনেকটা বন্দুকের ট্রিগারের মতো। গুলি একবার বের হয়ে গেলে সেইকে যেমন আর ব্যবহার করা যায় না, তেমনি সূতাটি একবার নিক্ষেপ করলে সেটাকে আর নিডোসাইটে ফিরিয়ে আনা যায় না। এ ধরনের নিডোসাইট খাদ্যবস্তুর সাথে হজম হয়ে যায়। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নতুন নিডোসাইট সৃষ্টি হয়।
নেমাটোসিস্টের সুত্রক নিক্ষেপ একইসাথে একটি রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। শিকারের বা শত্রুর সন্ধান অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিডোসাইট উদ্দীপ্ত হলে এ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। কোনো শিকার ????????????????????-র কর্ষিকার নিকটবর্তী হলে শিকার-দেহের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে নেমাটোসিস্ট প্রাচীরের পানিভেদ্য ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে থলির ভিতরে দ্রুত পানি প্রবেশ করায় ভিতরের অভিস্রবণিক চাপও বেড়ে যায়। এসময় শিকার নিডোসাইটের নিডোসিল স্পর্শ করামাত্র এর অপারকুলাম খুলে যখন দ্রুত পানি ভিতরে প্রবেশ করায় হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ (hydrostatic pressure) বেড়ে গেলে নেমাটোসিস্ট-সূত্রক ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।
নেমাটোসিস্টের সুত্রক নিক্ষেপ যুগপৎভাবে একটি রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। শিকারের বা শত্রুর সন্ধান অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিডোসাইট উদ্দীপ্ত হলে এ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। কোনো শিকার ????????????????????-র কর্ষিকার নিকটবর্তী হলে শিকার-দেহের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে নেমাটোসিস্ট প্রাচীরের পানিভেদ্য ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে থলির ভিতরে দ্রুত পানি প্রবেশ করায় ভিতরের অভিস্রবণিক চাপও বেড়ে যায়। এসময় শিকার নিডোসাইটের নিডোসিল স্পর্শ করামাত্র এর অপারকুলাম খুলে যখন দ্রুত পানি ভিতরে প্রবেশ করায় হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ (hydrostatic pressure) বেড়ে গেলে নেমাটোসিস্ট-সূত্রক ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।
মেসোগ্লিয়া (Mesogloea)
মেসোগ্লিয়া হলো হাইড্রার এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস এর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জেলীর মতো, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক স্তর। মেসোগ্লিয়া স্তরটি দেহ এবং কর্ষিকা উভয় স্থানে ছড়ানো থাকে। তবে কর্ষিকায় সবচেয়ে পাতলা এবং পাদ চাকতিতে সবচেয়ে বেশি পুরু হয়।
মেসোগ্লিয়ার এ ধরনের বিন্যাস পাদ-চাকতির অতিরিক্ত যান্ত্রিক প্রসারণ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং কর্ষিকাকে অধিকতর নমনীয়তা প্রদান করে। হাইড্রারমেসোগ্লিয়া প্রায় শূন্য দশমিক এক মাইক্রোমিটার পুরু হয় এবং উভয় স্তরের কোষ মেসোগ্নিয়া গঠনে অংশ গ্রহণ করে।
মেসোগ্লিয়ার কাজ:
- মেসোগ্লিয়া দেহকে সাপোর্ট করতে সহায়তা করে এবং এক ধরনের ইলাস্টিক কঙ্কাল হিসেবে কাজ করে।
- মেসোগ্লিয়া দুটি কোষস্তরের ভিত্তিরূপে কাজ করে।
- স্নায়ুকোষ ও সংবেদী কোষতন্তুসমূহ এবং পেশি-আবরণী কোষ সংকোচনশীল মায়োফাইব্রিল ধারণ করে।
- মেসোগ্লিয়ায় অবস্থিত পেশি-আবরণী কোষের সংকোচনশীল মায়োফাইব্রিলের সংকোচনে দেহ বা কর্ষিকা খাটো হয়। ফলে দেহ বাঁকানো সম্ভব হয়।
গ্যাস্ট্রোডার্মিস বা অন্তঃত্বক
গ্যাস্ট্রোডার্মিসের গঠন অনেকটা সরল এবং এটি পাঁচ ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত। যেমন- পুষ্টি বা পেশি-আবরণী,গ্রন্থি কোষ, ইন্টারস্টিশিয়াল, সংবেদী এবং স্নায়ু কোষ।
১। পুষ্টি কোষ বা পেশি-আবরণী কোষ:
গ্যাস্ট্রোডার্মিসের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে পুষ্টি কোষ অবস্থিত। প্রতিটি কোষ স্তম্ভাকার এবং একটি বড় নিউক্লিয়াস ও গহ্বরযুক্ত। এসব কোষের সংযুক্ত প্রান্ত থেকে সূক্ষ, সংকোচনশীল তন্তুবিশিষ্ট পেশি প্রবর্ধন সৃষ্টি হয়ে মেসোগ্লিয়ার সমকোণে অবস্থান করে।
ভেতরের মুক্ত প্রান্তের গঠনের উপর ভিত্তি করে দুভাগে ভাগ করা যায়।
- ফ্ল্যাজেলীয় কোষ – ফ্ল্যাজেলীয় কোষ গুলোর মুক্ত প্রান্তে ১-৪টি সুতার মতো ফ্লাজেলা সংযুক্ত থাকে।
- ক্ষণপদীয় কোষ- ক্ষণপদীয় কোষগুলোর মুক্ত প্রান্ত ক্ষণপদযুক্ত।
পুষ্টি কোষ বা পেশি-আবরণী কোষের কাজ:
- পেশি প্রবর্ধনগুলো সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহকে সরু ও মোটা করে।
- মুখ ও কর্ষিকার গোড়ায় অবস্থিত পেশি-প্রবর্ধনগুলো নিজের ছিদ্র বন্ধ করতে স্ফিংক্টার-এর মতো কাজ করে।
- ফ্ল্যাজেলীয় কোষের ফ্ল্যাজেলা আন্দোলিত হয়ে খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।
- পেশি কোষ প্রয়োজনে আন্দোলিত হয়ে মুখছিদ্র পথে পানি প্রবেশ করায়।
- ক্ষণপদীয় কোষের ক্ষণপদ খাদ্যকণা গলাধঃকরণ করে অন্তঃস্থ খাদ্যগহ্বরে পরিপাক করে।
২। গ্রন্থি কোষ (Gland cell)
গ্রন্থিকোষগুলো পুষ্টিকোষের ফাঁকে ফাঁকে এলোমেলো ভাবে অবস্থান করে। এগুলোর সংখ্যা মূল দেহ এবং হাইপোস্টোমে সবচেয়ে বেশি থাকে। আবার পদতলে অল্প পরিমাণে থাকলেও কর্ষিকায় থাকে না।
গ্রন্থিকোষগুলো দুরকম হয়ে থাকে। যেমনঃ
- মিউকাস ক্ষরণকারী– এগুলো প্রধানত হাইপোস্টোম অঞ্চলে অবস্থান করে এবং পিচ্ছিল মিউকাস ক্ষরণ করে।
- এনজাইম ক্ষরণকারী- অন্যান্য স্থানের কোষগুলো এ ধরনের হয়ে থাকে। যার থেকে পরিপাকের জন্য এনজাইম ক্ষরিত হয়। হাইপোস্টোমের গ্রন্থিকোষের কাজ হচ্ছে নিঃসৃত মিউকাস খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল করে গিলতে সাহায্য করা।
৩। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial cell)
ইন্টারস্টিশিয়াল কোষগুলোপেশি আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে এসব কোষ এপিডার্মিস থেকে আগত কোষ। এসব কোষ গোল বা ত্রিকোণাকার এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস,মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, মুক্ত রাইবোসোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া বহন করে।
ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের কাজ:
- এন্ডোডার্মিসের প্রয়োজনীয় যে কোনো কোষ গঠন করাই এর কাজ।
৪। সংবেদী কোষ (Sensory cell)
সংবেদী কোষগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত। প্রতিটি কোষ লম্বা ও সরু। এসব কোষের মুক্ত প্রান্ত থেকে বের হওয়া সূক্ষ সংবেদী রোম সিলেন্টেরণে উৎপন্নহয় এবং মেসোগ্লিয়ার সাথে লাগানো প্রান্ত থেকেবের হওয়া রোম স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত থাকে।
সংবেদী কোষের কাজ
- পানির সাথে সিলেন্টেরণে প্রবেশিত খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থের গুণাগুণ যাচাই করে স্নায়ুকোষে পাঠায়
৫। স্নায়ু কোষ (Nerve cell)
সাধারণত স্নায়ু কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থান করে। এরা সংখ্যায় খুব কম। এসব কোষের নির্দিষ্ট আকার নেই। একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক সূক্ষ শাখান্বিত তন্তু নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে স্নায়ু জালিকা গঠন করে।
স্নায়ু কোষের কাজ
স্নায়ু কোষের কাজ হলো সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা স্থানান্তর করা।
সিলেন্টেরন-
Hydra-র দেহের কেন্দ্রে অবস্থিত ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসে আবৃত ফাঁকা গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। সিলেন্টেরনকে অনেক সময় ব্লাইন্ড গাট বা ব্লাইন্ড স্যাক বলা হয়। খাদ্যের বহিঃকোষীয় পরিপাক, খাদ্যসার, শ্বসন, রেচন পদার্থ এই একটি মাত্র ছিদ্র দিয়ে পরিবাহিত হয়।
হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক
হাইড্রার খাদ্য
অন্যান্য সকল প্রাণীর মতো হাইড্রাও খাদ্য গ্রহণ করে হাইড্রা মাংসাশী (Carnivorous) প্রাণী। পানিতে থাকা বিভিন্ন প্রাণীদের মাংস খেয়ে এরা বেঁচে থাকে। যে সব ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে নেমাটোসিস্ট দিয়ে সহজে কাবু করা যায়, সে সব প্রাণীই হাইড্রার প্রধান খাদ্য। যেমনঃ বিভিন্ন পতঙ্গের লার্ভা, সাইক্লোপস (Cyclops) ও ড্যাফনিয়া (Daphnia) ছোট ছোট কৃমি, মাছের ডিম এবং এনিলিডা পর্বের খন্ডায়িত প্রাণী। ক্ষুদ্র ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী হাইড্রার প্রধান খাবার।
হাইড্রার খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি
ক্ষুধার্ত Hydra নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে মূলদেহ ও কর্ষিকাগুলো ভাসিয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কোনো শিকার কাছে আসা মাত্রই কর্ষিকার নেমাটসিস্টগুলো সাথে সাথে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং ঐ শিকার কর্ষিকা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট-সূত্র নিক্ষেপ করে।
ভলভেন্ট নেমাটসিস্ট এর সুতা শিকারকে জড়িয়ে ধরে এবং নড়তে দেয় না। কর্ষিকায় অবস্থিত গ্ল্যুটিন্যান্টগুলো থেকে আঠালো রস বের হয় যা শিকারকে সহজে আটকে ফেলে। স্টিনোটিল নেমাটসিস্ট তখন শিকারের দেহে হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে শিকারের দেহকে অবশ করে দেয়। এরপর কর্ষিকা শিকারকে মুখের কাছে নিয়ে আসে এবং মুখছিদ্র স্ফিত ও চওড়া হয়ে সেটিকে সরাসরি মুখে ঢুকিয়ে খেয়ে ফেলে। প্রন্থি কোষ থেকে নিঃসৃত মিউকাসে সিক্ত ও পিচ্ছিল হয় এবং হাইপোস্টোম ও দেহ প্রাচীরের সংকোচন- প্রসারণের ফলে খাদ্য সিলেন্টেরনে পৌছায়।
হাইড্রার খাদ্য পরিপাক
যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে তরল, সরল ও কোষের শোষণ উপযোগী অণুতে পরিণত হয়, তাকে পরিপাক বলে।
হাইড্রার মুখছিদ্রের চারদিকে অবস্থিত পেশী-আবরণী কোষ প্রসারিত হয়েমুখছিদ্র খুলে যায়। এসময় কর্ষিকার সাহায্যে খাদ্য মুখের ভিতর দিয়ে সিলেন্টেরণে প্রবেশ করলে সিলেন্টেরণে খাদ্য পরিপাক হয়।
Hydra-র খাদ্য পরিপাকের সময় অন্তঃত্বকের গ্রন্থিকোষ থেকে এনজাইম এবং মিউকাস নিঃসৃত হয়। ফ্লাজেলাযুক্ত পেশী আবরণী কোষ সমূহের ফ্লাজেলা আন্দোলনের দ্বারা সিলেন্টেরণের মধ্যে জীবিত খাদ্য মারা যায় ও কিছুটা চূর্ণ বিচূর্ণ হয় এবং উৎসেচক ও মিউকাসের সাথে মিশ্রিত হয়। ফলে সিলেন্টেরণের মধ্যে খাদ্য আংশিক পরিপাক হয়।
পরিপাক দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়। যেমন-
বহিঃকোষীয় পরিপাক (Extracellular digestion)
কোন নির্দিষ্ট কোষের অভ্যন্তরে পরিপাক না হয়ে কোষের বাইরে কোন নালী বা থলির মধ্যে যে পরিপাক সংঘটিত হয় তাকে আন্তঃকোষীয় বা বহিঃকোষীয় পরিপাক বলে।
হাইড্রার সিলেন্টেরণে আন্তঃকোষীয় বা বহিঃকোষীয় পরিপাক পদ্ধতিতে খাদ্যের কিছুটা পরিপাক ঘটে। সিলেন্টরণে এই আংশিক পরিপাককৃত খাদ্য এরপর ফ্যাগােসাইটোসিস পদ্ধতিতে হাইড্রার এন্ডােডার্মের ক্ষণপদযুক্ত পেশীআবরণী কোষসমূহে প্রবেশ করে। এই কোষের অভ্যন্তরে খাদ্যগহ্বরে খাদ্য জমা হয় ও পরিপাক হয়।
অন্তঃকোষীয় পরিপাক (Intracellular Digestion)
কোনও নির্দিষ্ট কোষের অভ্যন্তরে খাদ্য পরিপাক হওয়ার পদ্ধতিকে অন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে। হাইড্রার ক্ষণপদযুক্ত পেশী আবরণী কোষের অভ্যন্তরে অন্তঃকোষীয় পরিপাক ঘটে।
Hydra-এর পরিশোষণ (Absorption)
পরিপাককৃত সরল খাদ্য অর্থাৎ এ্যামাইনো এসিড, গ্লুকোজ এবং ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারল ক্ষণপদযুক্ত পেশী আবরণী কোষের সাইট্রোপ্লাজমে শোষিত হয়।
অপর পক্ষে অপাচ্য বর্জ্যপদার্থ পানির সাথে মুখছিদ্রের মাধ্যমে বের হয়ে যায়। সুতরাং হাইড্রার সিলেন্টেরণে আন্তঃ বা বহিঃকোষীয় এবং ক্ষণপদযুক্ত পেশী আবরণী কোষে অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পাদিত হয়।
Hydra-এর চলন
সব প্রাণীর জন্যই চলন একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া। প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলার জন্য, খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, বিনোদন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে প্রাণী চলনের মাধ্যমে স্থান ত্যাগ করে। নির্দিষ্ট চলন অঙ্গ না থাকায় সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিভিন্নভাবে প্রধানত পদতল, দেহের সংকোচন-প্রসারণশীল পেশিতন্তু ও তিন ধরনের নেমাটোসিস্টের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।
চলন প্রাণীর স্বতঃপ্রণােদিত হয়ে স্থান পরিবর্তন করার পদ্ধতি। খাদ্য, শিকার বা শত্রুর স্পর্শ জাতীয় উদ্দীপনা এক্টোডার্ম বা এন্ডোডার্মের সংবেদী কোষ সমূহের মাধ্যমে স্নায়ুকোষে সঞ্চারিত হয়।
স্নায়ুকোষের নির্দেশ অনুযায়ী পেশীকোষের পেশীলেজ সংকুচিত হয়। এরপর দেহের ও কর্ষিকার বিশেষ অঞ্চল প্রইয়োজনমত বেঁকে গিয়ে চলন সম্পাদিত হয়। এছাড়া পদচাকতি ও কর্ষিকাগুলো চলনে ভূমিকা রাখে।
হাইড্রায় আমরা বিভিন্ন ধরনের চলন দেখতে পাই। যেমন-
১। হামাগুড়ি বা লুপিং (Looping)
লম্বা দুরত্ব অতিক্রমের জন্য Hydra সাধারণত লুপিং চলনের আশ্রয় নেয়। এ পদ্ধতিতে একবার চলতে হাইড্রা একটিমাত্র ফাস বা লুপ তৈরি করে।
এক্টোডার্মের পেশী আবরণী কোষের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে হাইড্রা লুপিং পদ্ধতিতে চলাচল করে। এ পদ্ধতিতে হাইড্রা তার দেহের অগ্রভাগকে গতিপথের দিকে হেলিয়ে দেয়। এসময় কর্ষিকাগুলো গতিপথকে আঁকড়ে ধরে। তখন হাইড্রা পাচাকতির উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়।
এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে হাইড্রার স্থানান্তর ঘটে। তাছাড়া এপদ্ধতিতে সব সময় হাইড্রার পদচাকতি মাটিতে সংলগ্ন থাকে, কখনও মুক্ত হয়ে উপরে ওঠে না। এ চলনে সব সময় কৰ্ষিকা সামনে ও পদচাকতি তার পিছনে অনুগামী হয়।
২। সমারসল্টিং (Somersaulting) বা ডিগবাজী
Hydra-র সাধারণ ও দ্রুত চলন প্রক্রিয়া হচ্ছে সমারসল্টিং। এই চলনের সময় দুইবার লুপ তৈরী হয়। এই পদ্ধতিতে চলনকে সমারসলটিং (Saumersalting) চলন বলে।
হাইড্রার দেহের একদিক সংকুচিত ও তার বিপরীত দিক প্রসারিত করে দেহকে বাঁকা করে চলনপথের ভূমির উপরে কর্ষিকাগুলো স্থাপন করে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে Hydra দেহকে বাঁকিয়ে গ্লুটিন্যান্ট জাতীয় নেমাটসিস্টের আঠালো রসের সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। এবং ডিগবাজী খেয়ে দ্রুত চলাচল করে।
তারপর পদচাকতিকে বিমুক্ত করে প্রায় ১৮০° কোণে বাকিয়ে চলন পথের উপরে চলনের অগ্রদিকে নতুন অবস্থানে স্থাপন করে। এরপর হাইড্রা কর্ষিকাগুলোকে বিমুক্ত করে পদচাকতির উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া এ পদ্ধতিতে একবার পদচাকতি সামনে ও কর্ষিকা পিছনে অবস্থান করে এবং তারপরের বার কর্ষিকা সামনে ও পদচাকতি পিছনে চলন তলের উপর সংলগ্ন হয়।
৩। গ্লাইডিং (Gliding) বা অ্যামিবয়েড চলন
গ্লাইডিং চলন প্রক্রিয়ায় Hydra পদতলের বহিঃত্বকীয় কোষগুলো থেকে পিচ্ছিল এক ধরনের রস ক্ষরণ করে। পরে ঐ স্থান থেকেই কোষীয় ক্ষণপদের অ্যামিবয়েড চলনের সাহায্যে হাইড্রা খুব আস্তে আস্তে ধীরগতিতে খুব সামান্য পথ অতিক্রম করে।
হাইড্রার পদচাকতির গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত পিচ্ছিল রসে চলনতলকে পিচ্ছিল করে হাইড্রা গ্লাইডিং বা এমিবয়েড চলন সম্পন্ন করে।এসময় পদচাকতির ক্ষণপদযুক্ত কোষের ক্ষণপদগু ব্যবহৃত হয়।
৪। ভাসা (Floating)
পাদ-চাকতির বহিঃত্বকীয় কোষ থেকে গ্যাসীয় বুদবুদ সৃষ্টি করে, ফলে প্রাণী ভিত্তি থেকে বিচ্যুত, হালকা ও উপুড় হয়ে পানির পৃষ্ঠতলে ভেসে উঠে।
৫। সাঁতার (Swimming)
কর্ষিকাগুলোকে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করে এবং দেহকে ভিত্তি থেকে মুক্ত করে Hydra সহজেই দেহকে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করে সাঁতার কাটতে পারে।
৬। হামাগুড়ি (Crawling)
এ প্রক্রিয়ায় Hydra কর্ষিকার সাহায্যে কাছাকাছি কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরে। পরে পাদ-চাকতি মুক্ত ও কর্ষিকা সংকুচিত করে পাদ-চাকতিকে নতুন জায়গায় স্থাপন করে। এ প্রক্রিয়ায় Hydra-র আরোহণ ও অবরোহণ সম্পন্ন হয়।
৭। হাঁটা (Walking)
এ ক্ষেত্রে Hydra তার দেহের ভার পাদ-চাকতির উপর না রেখে কর্ষিকার উপর স্থাপন করে এবং কর্ষিকাকে পায়ের মতো ব্যবহার করে উল্টোভাবে ধীর গতিতে চলতে পারে।
৮। দেহ সংকুচিত (খাটো) বা প্রসারিত (লম্বা) করে
হাইড্রাকে স্পর্শ করলে এর দেহের পেশী-আবরণী কোষের সংকোচনের মাধ্যমে দেহকে সংকুচিত করে বলের মত আকৃতি ধারণ করে।
এক্টোডার্মের পেশী আবরণী কোষের পেশীলেজ আড়াআড়িভাবে মেসোগ্লিয়ার মধ্যে বিস্তৃত থাকে। এক্টোডার্মের পেশীলেজের সংকোচনে দেহ খাটো ও মোটা এবং এন্ডোডার্মের পেশীলেজের সংকোচনে দেহ সরু ও লম্বা হয়। এভাবে দেহের সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা হাইড্রা চলন সম্পন্ন করে।
৯। দেহকে বাঁকা করে ও কাঁত হয়ে বা হেলে দুলে
খাদ্যবস্তু ক্ষুধার্ত হাইড্রার সংস্পর্শে এলে হাইড্রা দেহকে বাঁকা করে কর্ষিকা দিয়ে খাদ্যবস্তুকে ধরে। এসময় দেহের একপাশের পেশী আবরণী কোষগুলো সংকুচিত ও তার বিপরীত দিকের পেশী আবরণী কোষগুলো প্রসারিত হয়ে দেহেকে হেলিয়ে দুলিয়ে বা বাঁকা ও কাত করে চলন সম্পন্ন করে।
হাইড্রার জনন
জনন হচ্ছে বংশবৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া। জীব তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহার করে।
হাইড্রার বংশবৃদ্ধির জন্য দুই ধরনের জনন হয়।
যৌন জনন:
যৌন প্রজনন ও স্ত্রী এবং পুরুষ জননাঙ্গ অর্থাৎ শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয় থেকে যথাক্রমে পুরুষ ও স্ত্রী জনন কোষ অর্থাৎ শুক্রাণু বা ডিম্বাণু সৃষ্টি এবং তাদের নিষেকের মাধ্যমে শিশু জীব উৎপাদন করার প্রক্রিয়াকে যৌন প্রজনন বলে। হাইড্রা জননকোষ সৃষ্টির মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন করে।
অযৌন জনন (Asexual reproducetion) :
যে প্রক্রিয়ায় জননকোষ অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বাণু ছাড়াই প্রাণী বংশবিস্তার করে তাকে অযৌন জনন বলে। হাইড্রা মুকুলোদগম ও দ্বিবিভাজনের মাধ্যমে এর অযৌন জনন সম্পন্ন করে।
মুকুলোদগম (Budding)
মুকুলোদগম অযৌন জননের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। গ্রীষ্মকালে যখন হাইড্রা পর্যাপ্ত খাবার পায় তখন মুকুল তৈরীর মাধ্যমে এই জননের শুরু হয়। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ পেশি-আবরণি কোষের ভেতরে ফাঁকে ফাঁকে গুচ্ছাকারে থাকে এবং স্ফীত হয়ে নতুন মুকুল তৈরি করে।
মুকুলোদগম বর্ণনা (Budding)
মুকুল গঠন প্রক্রিয়া কয়েকটা ধারাবাহিক ধাপে ঘটে। যথাঃ
- হাইড্রার দেহকান্ডের নীচের দিকে এক্টোডার্মের এক বা একাধিক স্থানের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ মাইটোসিস পদ্ধতিতে বারবার বিভাজিত হয়। ফলে এ সকল স্থানে কিউটিকলের নীচে একটা করে নিরেট ও স্ফীত প্রবৃদ্ধি বা অংশ গঠিত হয়।
- এই প্রবৃদ্ধিগুলো ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে এবং এর ভিতরে মাতৃ হাইড্রার সিলেন্টেরন প্রসারিত হয়। ফলে প্রবৃদ্ধিটি একটা দ্বিস্তর বিশিষ্ট ফাপা ও নলাকার গঠনরত মুকুলে পরিণত হয়।
- এই গঠনত মুকুলের অগ্রপ্রান্তে এরপর একে একে হাইপোস্টোম, কর্ষিকা এবং মুখছিদ্র গঠিত হয়।
- প্রায় একই সাথে গঠনরত মুকুল ও মাতৃহাইড্রার সংযোগস্থলে একটা খাঁজ গঠিত হয় এবং তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।
- মুখছিদ্র গঠিত হবার পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ দশার মুকুলে খাজটি গভীরতর হতে হতে এক সময় মাতৃ হাইড্রার দেহ থেকে বিছিন্ন হয়ে যায়।
Hydra-এর বিভাজন
কোনো কারণে হাইড্রার দেহ দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেকটি খণ্ড থেকে নতুন হাইড্রা সৃষ্টি হয়। এটিই হাইড্রার বিভাজন বা পুনরুৎপত্তি বলে।
বিভাজন কোনো স্বভাবিক জনন প্রক্রিয়া না। কারণ এটি হঠাৎ সংঘটিত হয়। এই পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার জন্যই হাইড্রাকে অমর প্রাণী বলা হয়।
মৃত্যু না হলেও এদের দেহ বিভাজিত হয়। বিভাজন দুভাবে হতে পারে, অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন আর অনুপ্রস্থ বিভাজন।
অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন:
হাইড্রার দেহ কোনো কারণে লম্বালম্বি দুই বা ততোধিক খন্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খন্ড থেকে পৃথক হাইড্রার উৎপত্তি হয়।
অনুপ্রস্থ বিভাজন:
যে প্রক্রিয়ায় হাইড্রার দেহ অনুপ্রস্থভাবে একাধিক খন্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খন্ড থেকে পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ায় নতুন হাইড্রা জন্ম লাভ করে তাকে অনুপ্রস্থ বিভাজন বলে।
হাইড্রার যৌন জনন
হাইড্রা শীতের প্রাক্কালে যৌন প্রজনন পদ্ধতিতে বংশ বৃদ্ধি করে। হাইড্রার স্থায়ী জননাঙ্গ থাকে না। প্রধানত শরৎকালে খাদ্য স্বল্পতার মতো প্রতিকূল পরিবেশে এদের দেহে অস্থায়ী জননাঙ্গের সৃষ্টি হয়। এদের পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গকে যথাক্রমে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় বলে। পরে শুক্রাশয়ে শুক্রাণু এবং ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু গঠিত হয়ে হাইড্রায় যৌন প্রজনন ঘটে। Hydra vulgaris একটা উভয়লিঙ্গিক (Bisexual) প্রাণী।
কিন্তু শুক্রাণু ও ডিম্বাণু পৃথক পৃথক সময়ে পরিপক্ক হয় বলে হাইড্রায় স্বনিষেক হয় না, পরনিষেক হয়। হাইড্রার যৌন প্রজনন প্রধান তিনটা ধাপে সম্পন্ন হয়। যথাঃ
১) গ্যামেটোজেনেসিস
জনন কোষ বা শুক্রাণু ও ডিম্বাণু গঠন প্রক্রিয়াকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। গ্যামেটোজেনেসিস দুই ধরনের হয়। যথাঃ (ক) স্পার্মাটোজেনেসিস ও (খ) উত্তজেনেসিস।
ক) স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis) শুক্রাণু গঠন প্রক্রিয়া
শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস বা শুক্রাণুজনন বলে।
- প্রজনন ঋতুতে দেহের উপরের অর্ধেকে এক বা একাধিক মোচার মতো শুক্রাশয় সৃষ্টি হয়। এর ভেতরে অসংখ্য শুক্রাণু থাকে।
- শুক্রাশয়ের ভেতরের ইন্টারিস্টিশিয়াল কোষ বারবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে স্পার্মাটোগোনিয়া সৃষ্টি করে।
- স্পার্মাটোগোনিয়া বড় হয়ে স্পার্মাটোসাইটে পরিণত হয়।
- স্পার্মাটোসাইট মিয়োসিস বিভাজনের ফলে ৪টি করে হ্যাপ্লয়েড স্পার্মাটিড উৎপন্ন করে।
- প্রত্যেকটি স্পার্মাটিড একেকটি শুক্রাণুতে পরিণত হয়।
- পরিণত শুক্রাণুতে স্ফিত মাথা, মধ্যখন্ড এবং একটি সরু লেজ থাকে।
খ) উওজেনেসিস (Ogenesis) বা ডিম্বাণু গঠন প্রক্রিয়া
ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস বা ডিম্বাণুজনন বলে।
- প্রজনন ঋতুতে দেহের নিচের দিকে একটি বা দুটি গোলাকার ডিম্বাশয় সৃষ্টি হয়।
- মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ইন্টারিস্টিশিয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে উওগোনিয়া তৈরী করে।
- এগুলোর মধ্যে একটি কোষ বড় হয়ে উওসাইটে পরিণত হয় এবং ছোট কোষগুলোকে খেয়ে ফেলে
- এটি তখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটিয়ে ৩টি ক্ষুদ্র পোলার বডি ও ১টি বড় সক্রিয় উওটিড সৃষ্টি করে।
- উওটিডটি রূপান্তরিত হয়ে ডিম্বাণুতে পরিণত হয় এবং পোলার বডিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়।
২) নিষেক ও জাইগোট গঠন
যৌন জননের দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে নিষেক।
- পরিণত শুক্রাণু, ডিম্বাণুর সন্ধানে ঝাঁকে ঝাঁকে পানিতে সাঁতরাতে থাকে।
- একাধিক শুক্রাণু ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ করলেও একটি মাত্র শুক্রাণুর নিউক্লিয়সই ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হয়ে নিষেক সম্পন্ন করে।
- শুক্রাণু ও ডিম্বানুর এই একসাথে মিলিত হওয়ার ফলে একটি ডিপ্লয়েড জাইগোট তৈরি হয়।
৩) পরিস্ফুরণ ও শিশু হাইড্রার জন্ম লাভ
সর্বশেষ ধাপটি হলো পরিস্ফুটন। জাইগোট থেকে শিশু হাইড্রার উৎপত্তি হওয়াকেই পরিস্ফুটন বলে। হাইড্রার পরিস্ফুটনে চারটি ধাপ দেখা যায়। মরুলা, ব্লাস্টুলা, গ্যাস্ট্রুলা এবং হাইড্রুলা।
মরুলা:
জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বরাবর বিভাজিত বহুকোষী, নিরেট ও গোলাকার কোষে পরিণত হয়, এটাই মরুলা।
ব্লাস্টুলা:
মরুলার কোষগুলো একস্তরে সজ্জিত হয়ে একটি ফাঁপা, গোল ভ্রূণে পরিণত হয়। এর নাম ব্লাস্টুলা। ব্লাস্টুলার কোষগুলোকে ব্লাস্টোমিয়ার এবং কেন্দ্রে ফাঁকা গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল বলে।
গ্যাস্ট্রুলা:
ব্লাস্টুলা গ্যাস্ট্রুলেশন প্রক্রিয়ায় দ্বিস্তরবিশিষ্ট গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত হয়। এটি এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও আদি সিলেন্টেরন নিয়ে গঠিত। গ্যাস্ট্রুলার চারদিকে কাইটিন নির্মিত কাঁটাযুক্ত সিস্ট আবরণী গঠিত হয়। সিস্টবদ্ধ ভ্রূণ মাতৃহাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জলাশয়ের তলদেশে চলে যায়।
হাইড্রুলা:
বসন্তের শুরুতে অনুকূল তাপমাত্রায় সিস্টের মধ্যেই ভ্রূণটি ক্রমশ লম্বা হতে থাকে। ভ্রূণের এ দশাকে হাইড্রুলা বলে। এ দশায়ই ভ্রূণে হাইপোস্টোম, মুখছিদ্র, কর্ষিকা আর পাদচাকতি গঠিত হয়। হাইড্রুলা সিস্টের আবরণী ছিড়ে পানিতে বের হয়ে আসে আর স্বাধীন জীবন-যাপন করে।
হাইড্রার শ্রমবন্টন
বহুকোষী জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্রের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর সুষম বণ্টনকে শ্রমবণ্টন বুঝায়। বহুকোষী প্রাণী হলেও অন্যান্য প্রাণীর মতো হাইড্রার দেহে অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয়নি। তাই কোষগুলো এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস স্তরে বিন্যস্ত থেকে এককভাবে পৃথক পৃথক কার্য সম্পাদন করে। নিডারিয়া পর্বের প্রাণীতে সর্বপ্রথম কোষের গঠনমূলক বৈষম্য ও শ্রমবণ্টন দেখা যায়।
কোষভিত্তিক শ্রমবণ্টন
এপিডার্মিস ও গ্যাসট্রোডার্মিসে অবস্থিত কোষগুলো এককভাবে আলাদা আলাদা কাজ করাকে কোষ ভিত্তিক শ্রমবন্টন বলে।
১। পেশি-আবরণী কোষ:
একদিকে দেহের আবরণ হিসেবে এবং অন্যদিকে পেশির মতো সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে কাজ করে বলে এসব কোষকে “পেশি-আবরণী কোষ” বলা হয়ে থাকে।
২। ইন্টারিস্টিশিয়াল কোষ:
এই কোষই হাইড্রার পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা তৈরী করে যার জন্য হাইড্রাকে অমর প্রাণী বলা হয়।
৩। নিডোসাইট:
একাধারে আত্নরক্ষা, শিকার ও চলনে এই কোষ ব্যবহৃত হয়।
৪। সংবেদী কোষ:
এই কোষ পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা, আবেশ বা অনুভূতি যেমন আলো, তাপ, স্পর্শ এসব গ্রহণ করে সরাসরি স্নায়ুকোষে সরবরাহ করে।
৫। স্নায়ু কোষ:
স্নায়ু কোষ সাধারণত সংবেদী কোষ থেকে উদ্দীপনা সংগ্রহ করে স্নায়ু জালকের সাহায্য দেহের বিভিন্ন অংশে সেই উদ্দীপনা পাঠায়।
৬। গ্রন্থিকোষ:
গ্যাস্ট্রোডার্মিসের গ্রন্থিকোষ বিভিন্ন রকম পদার্থ ক্ষরণ করে বিভিন্ন রকম কাজ। পাদ-চাকতিতে উপস্থিত গ্রন্থিকোষ মিউকাস ক্ষরণ করে হাইড্রাকে কোন বস্তুর সাথে আটকে থাকতে সহায়তা করে। ক্ষণপদ সৃষ্টি করে চলতে সাহায্য করে। বুদবুদ গঠনের মাধ্যমে হাইড্রাকে ভাসতে সাহায্য করে এবং মুখছিদ্রের গ্রন্থিকোষ খাদ্য গলাধঃকরণে সাহায্য করে।
৭। পুষ্টি-পেশিকোষ:
কোষের ভেতরের ও বাহিরের পরিপাক সম্পন্ন করে।
কার্যভিত্তিক শ্রমবণ্টন
কার্যভিত্তিক শ্রমবণ্টনে হচ্ছে হাইড্রার দেহে উপস্থিত বিভিন্ন অঙ্গগুলো আলাদাভাবে যে কাজ করে।
১। মুখছিদ্রঃ
খাদ্য গ্রহণ ও বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে দায়িত্ব পালন করে।
২। সিলেন্টেরনঃ
একাধারে পরিপাক ও পরিবহন গহ্বর হিসেবে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পাদন করে।
৩। কর্ষিকাঃ
কর্ষিকা হাইড্রার আত্মরক্ষা, শিকার ধরা, চলন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪। পাদ-চাকতিঃ
পাদ-চাকতি মূলত কোন বস্তুর সাথে হাইড্রাকে আটকে থাকতে এবং চলতে সহায়তা করে।
৫। দেহকাণ্ডঃ
দেহকাণ্ড সাধারণত জনন অঙ্গ এবং মুকুল ধারণ করে।
হাইড্রার মিথোজীবিতা
মিথোজীবিতা গ্রিক শব্দ Symbioum থেকে এসেছে। গ্রিক শব্দ সিমবায়োমের অর্থ হচ্ছে Live Together. অর্থাৎ একসাথে থাকাকে সিমবায়োসিস বলে।
যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সাহচর্যকে মিথোজীবিতা বলে। এ অবস্থায় জীবদুটিকে মিথোজীবী (Symbiont) বলা হয়। মিথোজীবিতাকে আবার Symbiosis এবং মিথোজীবিদের Symbiont ও বলা হয়।
Hydra viridissima নামক সবুজ হাইড্রা ও Zoochlorella নামক শৈবালের মধ্যে এ সম্পর্ক সুস্পষ্ট দেখা যায়। Zoochlorella বা সবুজ শৈবাল হাইড্রাকে সবুজ বর্ণ দান করে এবং এজন্যই হাইড্রা ভিরিডিসিমা বাইরে থেকে দেখতে সবুজ দেখায়।
মিথোজীবী হাইড্রা এবং জুওক্লোরেলার(শৈবাল) পারস্পরিক উপকার সাধনের বিবরণ
হাইড্রা কিভাবে উপকৃত হয়?
খাদ্যঃ
সালোকসংশ্লেষণে শৈবালের উৎপাদিত শর্করা জাতীয় খাদ্যের উদবৃত অংশ হাইড্রা খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে ।হাইড্রা মৃত শৈবাল কেও খাদ্য হিসেবে গ্রহন করে।
শ্বসনঃ
শৈবালের সালোকসংশ্লেষণে সৃষ্ট অক্সিজেন হাইড্রার শ্বসনে ব্যবহিত হয় ।
কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণঃ
হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ঠ কার্বন ডাইঅক্সাইড শৈবাল গ্রহন করে হাইড্রাকে ঝামেলা মুক্ত করে ।
শৈবাল কীভাবে উপকৃত হয়?
আশ্রয়ঃ
শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মাল পেশি-আবরনী কোষে নিরাপদ আশ্রয় ও সুরক্ষা লাভ করে ।
সালোকসংশ্লেষণঃ
হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড কে শৈবাল সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে।
খাদ্যেৎপাদনঃ
হাইড্রার বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থকে শৈবাল আমিষ তৈরির বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে।